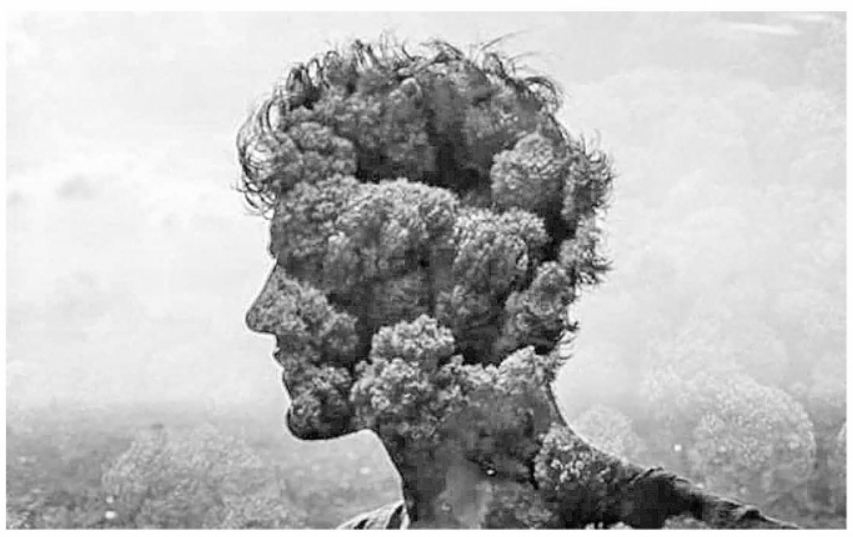আ রা ফা ত র হ মা ন
২০২১ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘বাস্তুতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা’। বাস্তুতন্ত্র হচ্ছে জৈব, অজৈব পদার্থ ও বিভিন্ন জীবসমন্বিত এমন প্রাকৃতিক একক যেখানে বিভিন্ন জীবসমষ্টি পরস্পরের সাথে এবং তাদের পারিপার্শ্বিক জৈব ও অজৈব উপাদানের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জীবনধারা গড়ে তোলে। প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্রে মূলত তিনটি উপাদান রয়েছে, যথা জড় উপাদান, ভৌত উপাদান ও জীবজগতের উপাদান। জড় উপাদানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা অজৈব বস্তু ও জৈব বস্তু। ক্ষুদ্র ও আণুবীক্ষণিক ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, শৈবাল ইত্যাদি থেকে শুরু করে জলে ভাসমান উদ্ভিদ ও ছোট-বড় স্থলজ উদ্ভিদ সবই উৎপাদক। পরিবেশের যেসব উপাদান খাদ্যের জন্য অন্য কোনো উপাদানের ওপর নিভর্রশীল নয়, তাকে উৎপাদক বলে। বাস্তুতন্ত্রে যেসব উপাদান উৎপাদকের তৈরি খাদ্য উপাদানের ওপর নিভর্রশীল, সেসব জীবকে খাদক বলে।
পরিবেশ বলতে কোনো ব্যবস্থার ওপর কার্যকর বাহ্যিক প্রভাবকসমূহের সমষ্টিকে বোঝায়। চারপাশের ভৌত অবস্থা, জলবায়ু ও প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য জীব ও জৈব উপাদান ইত্যাদির সামষ্টিক রূপই হলো পরিবেশ। পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের দ্বারাই একজন ব্যক্তি বা প্রাণী, এমনকি উদ্ভিদ প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই প্রভাবকসমূহের মধ্যে থাকে প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক বা কৃত্রিম পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহ। বিশ্ব পরিবেশ দিবস প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে পালিত দিবস। এই দিনটিতেই জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ কনফারেন্স হয়েছিল ১৯৭২ সালের ৫ থেকে ১৬ জুন অবধি। তখন থেকেই প্রতি বছর এই দিবস পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি প্রথম পালিত হয় ১৯৭৪ সালে। প্রতি বছরই দিবসটি আলাদা আলাদা প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পালিত হয়।
১৯৬৮ সালের ২০ মে জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদের কাছে একটি চিঠি পাঠায় সুইডেন সরকার। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল প্রকৃতি ও পরিবেশদূষণ সম্পর্কে তাদের গভীর উদ্বেগের কথা। সে বছরই জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি সাধারণ অধিবেশনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরের বছর জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সমাধানের উপায় খুঁজতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মতিতে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালের ৫ থেকে ১৬ জুন জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি ইতিহাসের প্রথম পরিবেশ-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের স্বীকৃতি পায়। ১৯৭৩ সালে সম্মেলনের প্রথম দিন ৫ জুনকে জাতিসংঘ ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা দেয়। ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছর দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে।
পরিবেশের উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে গাছপালা, নদী-নালা, খাল-বিল, রাস্তঘাট, ঘর-বাড়ি, পানি, সূর্য, মাটি, বায়ু, নৌকা, পশু-পাখি, বিদ্যালয়, দালানকোঠা ইত্যাদি তথা আমাদের চারপাশের সব কিছুই পরিবেশের অংশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে সেই পরিবেশ যা প্রকৃতি নিজে নিজে তৈরি করে। এগুলো হচ্ছে গাছ, পাহাড়-পর্বত, ঝরনা, নদী ইত্যাদি। এগুলো মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। এগুলো প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়। মানুষের তৈরি পরিবেশ হচ্ছে নগরায়ণ, বন্দর ইত্যাদি। এগুলো মানুষ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে তৈরি করে। পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের সুসমন্বিত রূপই হলো সুস্থ পরিবেশ। এই সুসমন্বিত রূপের ব্যত্যয়ই পরিবেশের দূষণ ঘটায় এবং পরিবেশের স্বাভাবিক মাত্রার অবক্ষয় দেখা দেয়। পরিবেশ বিভিন্ন কারণে দূষিত হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট কারণও এর সাথে দায়ী। পরিবেশদূষণের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ১২টি মারাত্মক রাসায়নিক উপাদানকে একত্রে ‘ডার্টি ডজন’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।
এদের মধ্যে ৮টি কীটনাশক অলড্রিন, ডায়েলড্রিন, ক্লোরডেন, এনড্রিন, হেপ্টাক্লোর, ডিডিটি, মিরেক্স, এবং টক্সাফেন; দুটি শিল্পজাত পিসিবি এবং হেক্সাক্লোরোবেনজিন এবং অন্য দুটো হলো কারখানায় উৎপন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত উপজাত: ডাইওক্সিন এবং ফিউরান। খাদ্যচক্রে প্রবেশ করে পৃথিবীব্যাপী সব পরিবেশের সব ধরনের জীবজন্তুর ওপর তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটায় এই বিষাক্ত পদার্থগুলো। ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম, ক্যানসার উৎপাদন, ভ্রূণ বিকাশের নানাবিধ সমস্যার মূলে দায়ী এই ডার্টি ডজন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই বিপন্ন পরিবেশের বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্তির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিবেশ আইন। মূলত পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের আইনই পরিবেশ আইন। এই আইন স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য বিশ্ব আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাগরিক ও সরকারি সংস্থাসমূহের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে। বিশ্ব পরিবেশের দ্রুত অবনতি হচ্ছে, বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে এ অবনতি হয়েছে আরো দ্রুত। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন পাস হয়েছে। কিন্তু জনবিস্ফোরণ, বনাঞ্চলের অবক্ষয় ও ঘাটতি এবং শিল্প ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবের দরুন দেশের পরিবেশ এক জটিল অবস্থার দিকে পৌঁছতে যাচ্ছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু পরিবেশনীতি প্রণয়ন ও নীতিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের পরিবেশ সমস্যাগুলো ব্যবস্থাপনায় জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে পরিবেশনীতি প্রণয়নের কৌশল অভিজ্ঞতাহীন একটি নতুন বিষয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রশাসন প্রক্রিয়া ও পরিবেশগত অগ্রাধিকারসমূহ শিল্পোন্নত বিশ্বের অনুরূপ বিষয়গুলি থেকেও অনেকটাই ভিন্ন। অধিকন্তু নীতি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের তীব্র অভাব কাজটিকে কঠিনতর করেছে। ভৌত ও আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বাংলাদেশকে টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার একটি পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র হিসেবে অভিহিত করা যায়। অত্যন্ত সীমিত সম্পদের ওপর প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত চাপ বস্তুত সম্পদ ও পরিবেশের সহনশীলতা উভয় বিবেচনায় দেশের ধারণ ক্ষমতাকে অতিক্রম করেছে।
গত তিন দশকে বনজ বৃক্ষের পরিমাণ ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে। কৃষিজমির প্রসার এবং বনজ দ্রব্যের বর্ধিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক বনভূমি অবৈধভাবে ফসলি জমিতে পরিণত করা হয়েছে, যদিও বন সম্পর্কিত হালনাগাদ পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। হিসাবে দেখা যায়, সত্তরের দশক থেকে বনভূমির পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭০ সালে মধুপুর অঞ্চলে ২০,০০০ একরেরও অধিক শালবন ছিল; বিশ বছর পর অবশিষ্ট থাকে আনুমানিক ১,০০০ একর। ১৯৯০ সালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে মাথাপিছু বনের পরিমাণ ০.০২ হেক্টরেরও কম যা বিশ্বে জনসংখ্যা অনুপাতে সর্বনিম্ন বনের পরিমাণগুলোর একটি।
বাংলাদেশের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে বন ও জলাভূমি এলাকায়। আনুমানিক ৫,০০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ বাংলাদেশে পাওয়া যায়। এ দেশে বাস করছে ২৬৬ ধরনের স্বাদু পানির ও ৪৪২ ধরনের সামুদ্রিক মাছ, ২২ উভচর, ১০৯ অভ্যন্তরীণ ও ১৭ সামুদ্রিক সরীসৃপ, ৩৮৮ স্থায়ী ও ২৪০ পরিযায়ী পাখি, ১১০ অভ্যন্তরীণ ও ৩ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। কিছু প্রজাতিকে হুমকির সম্মুখীন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশের জানা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে ১৩টি সম্প্রতি এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মৎস্য প্রজাতিসমূহের মধ্যে ৫৪টি হুমকির সম্মুখীন। বিপন্ন উভচর, অভ্যন্তরীণ সরীসৃপ, স্থায়ী পাখি ও অভ্যন্তরীণ স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতি সংখ্যা যথাক্রমে ৮, ৫৮, ৪১ ও ৪০।
জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হওয়ার প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে—মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে প্রাণীর বিচরণ পথ ও জলাভূমি আবাসস্থলের ক্ষতি; কৃষি, বাসস্থান ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মানুষের বনভূমি দখল; জ্বালানি ও নির্মাণের জন্য নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলে বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ হ্রাস; কতিপয় বনজসম্পদ যেমন ভেষজ উদ্ভিদ, বাঁশ ও বেতের অতিরিক্ত আহরণের ফলে রক্ষামূলক বাসস্থান লোপ; অতিরিক্ত বন্যপ্রাণী শিকার; উফশী জাতসমূহের একক চাষ বা বহুমুখী শস্য চাষ হ্রাস পাওয়ায় কৃষি রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি; ম্যানগ্রোভ বন উজাড় এবং জুমচাষ।
ঢাকায় অনেক ছোট-বড় শিল্প-কারখানা রয়েছে, যেখানে বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত এবং ক্ষতিকর বর্জ্য তৈরি হয় এবং পরিবেশের উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটায়। ঢাকায় রয়েছে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা যেখানে প্রতিদিন প্রায় ১৮,০০০ লিটার তরল এবং ১১৫ মে. টন কঠিন বর্জ্য জমা হয় এবং এসব বর্জ্য নিকটবর্তী নালা-নর্দমা ও বুড়িগঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। এসব বর্জ্যের মধ্যে সালফিউরিক এসিড, ক্রোমিয়াম, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম অক্সাইড ইত্যাদি রয়েছে। এগুলো মাটিতে শোষিত হয়ে ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ ঘটাতে পারে। এ ছাড়া তীব্র দুর্গন্ধ আশপাশের মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
পরিবেশ কার্যক্রমের দেশের সকল ভৌগোলিক অঞ্চল ও উন্নয়ন খাতে বিস্তার হয়েছে। তদনুযায়ী পরিবেশনীতির সামগ্রিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত বিভিন্ন কর্মকৌশলে ১৫টি খাত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন, শক্তি ও জ্বালানি, পানিসম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ, ভূমি, বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য, মৎস্য ও পশুসম্পদ, খাদ্য, উপকূলীয় ও সামুদিক পরিবেশ, পরিবহন ও যোগাযোগ, গৃহায়ন ও নগরায়ণ, জনসংখ্যা, শিক্ষা ও জনসচেতনতা এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা। পরিবেশনীতির ৪নং অনুচ্ছেদে রয়েছে আইনগত রূপরেখা, যাতে বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত নতুন আইন প্রণয়ন এবং সব আইন ও বিধান সংশোধন, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং পরিবেশদূষণ ও অবক্ষয়রোধ প্রভৃতি বিষয় শর্তাবদ্ধ হয়েছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিবেশ সুরক্ষা বাংলাদেশ সরকারের একটি অগ্রাধিকারী বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শহুরে ও গ্রামীণ পরিবেশের দ্রুত অবক্ষয় নিয়ে সরকার ও সুশীল সমাজের উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল একটি সুষ্ঠু জাতীয় নীতির মাধ্যমেই পরিবেশের প্রতি সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং পরিবেশ সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যা সমাধান সম্ভব। সরকার পরিবেশ নীতি গ্রহণসহ বেশকিছু নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। পরিবেশনীতির লক্ষ্য হলো : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাস্তুসংস্থানিক ভারসাম্য ও সার্বিক উন্নয়ন সুরক্ষা; প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশকে রক্ষা; পরিবেশদূষক ও ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ; সব খাতে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ; সব জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশ অনুকূল ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশ সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সঙ্গে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় কার্যকর সংযোগ রক্ষা।
লেখক : সহকারী কর্মকর্তা, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়