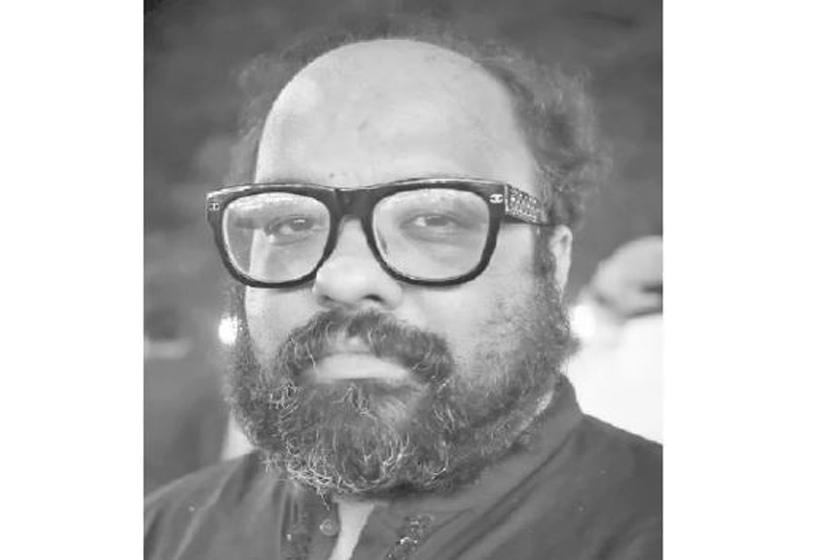সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ:
কিছুদিন পরপরই ফেসবুকে একটা আলাপ খুব জনপ্রিয়তা পায়, মধ্যবিত্তের অবস্থা খুব খারাপ। এতটাই যে, আসলে নিম্নবিত্তও ওদের চেয়ে ভালো আছে। এই আলাপটা বেশ জনপ্রিয় হয়, মধ্যবিত্ত হা-হুতাশ করে। কেউ কেউ বলে বসেন, ওরা তো চাইলে ভিক্ষা করতে পারে, আমরা তো তাও পারি না। এই আলাপে যতই আবেগ থাক তা কেবল ভুল নয়, বহু দিক দিয়ে সমস্যাজনক। গত সপ্তাহে ফেসবুকে এ ধরনের একটা পোস্ট ঘুরঘুর করছিল। সেটা দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাক।
সেই পোস্টের সারসংক্ষেপ হচ্ছে জনৈক মফিজ সাহেবের বাসার কাজের বুয়া রহিমা বেশ কয়েকটি বাসায় কাজ করে মাসে ১২ হাজার টাকা উপার্জন করেন। উনার স্বামী রিকশাচালক কুদ্দুস মাসে ২০ হাজার কামান আর ১২ বছরের ছেলে রুবেল টেম্পোর হেলপারি করে মাসে আয় করে ৬ হাজার টাকা। মোট ৩৮ হাজার টাকা। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা মফিজ একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে ২৮ হাজার টাকা বেতনে কাজ করেন। উনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম। একে তো কুদ্দুসের পরিবারের চেয়ে তার পরিবারের আয় কম, তদুপরি যেই বাসায় থাকেন তার ভাড়া রহিমাদের বস্তির বাসার চেয়ে অনেক বেশি। বাচ্চার খরচ আর সামাজিকতা তো আছেই।
অনেকে হা-হুতাশ করলেও একটা বড় অংশের মানুষই এই আলাপের অসারতা দেখান। একটা পরিবারের তিনজনের আয়ের সঙ্গে অপর পরিবারের একজনের আয়ের তুলনা সমীচীন নয়। রহিমা যদি কাজ করতে পারেন, মফিজের বউ কেন করবেন না? এর চেয়েও ভয়াবহ কথা হচ্ছে, একটা ১২ বছরের ছেলে পড়ালেখা বাদ দিয়ে কেন হেলপারি করবে? এই অসহায় বাচ্চাটাকে আবার হিংসাও করছে? মধ্যবিত্ত কি এতটাই অমানবিক হয়ে গেল? হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল?
মোটা দাগে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অফিসের ডেস্কে বসে কাজ করে আর নিম্নবিত্ত গতর খাটিয়ে কাজ করে এই ব্যাপারটা ধরে দুজনের কাজের সুবিধা আর অসুবিধা ব্যাখ্যা করা যাক। শারীরিক পরিশ্রম যারা করেন, তাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আয় কমতে থাকে। শরীরের বল কমে আসে বিধায় উনারা তরুণদের মতো কাজ পান না এবং করতে পারেন না। দীর্ঘদিন শারীরিক কাজ করার ফলে অল্প বয়সেই নানা রকম রোগব্যাধি হয়।
রিকশা চালানোর মতো পেশার ক্ষেত্রে শক্তি অনেক লাগে বিধায় উনাদের খাওয়া-দাওয়া বেশি করতে হয়। ফলে, যা আয় করেন তার বড় অংশ খাবারের পেছনেই দিতে হয়। যদিও এতে পুষ্টিকর খাবার মেলে না। ফলে, কর্মক্ষমতা কমতে থাকে এবং কর্ম বছর অনেক কম হয়। শিক্ষিত শ্রেণির অনেকেই বলেন, একজন রিকশাওয়ালা যদি দিনে ৭০০ টাকা উপার্জন করতে পারেন তবে তার মাসের আয় ২০ হাজার।
কিন্তু এখানে বড় দুটো সমস্যা আছে। রিকশার জমা ও রাস্তার নানা খরচাপাতি বাদ দিয়ে দিনে ৭০০ টাকা উপার্জন করতে হলে কমপক্ষে ১২০০ টাকা আয় করতে হবে। যদি ২০ মিনিটের একটা ট্রিপ মেরে ৪০ টাকা উপার্জন হয় (ঢাকার জ্যামে খুবই অনিশ্চিত) তবে ১২০০ টাকা আয় করতে পাটিগণিতের হিসাবে ৬০০ মিনিট বা দশ ঘণ্টা রিকশা চালাতে হবে।
এমনকি একজন বলিষ্ঠ তরুণের পক্ষেও দিনে দশ ঘণ্টা যাত্রীসহ রিকশা চালানো শারীরিকভাবে ভীষণ চ্যালেঞ্জের। তর্কের খাতিরে ধরলাম সে একদিন তা করল। কিন্তু টানা ৩০ দিন কি তা কোনোভাবে সম্ভব? বছরে ৩৬৫ দিনের তো প্রশ্নই ওঠে না। ঢাকা শহরে বহু রিকশাচালকের সঙ্গে কথা বলে আমার বোঝাপড়া হচ্ছে উনারা মাসে ১৮-২০ দিন রিকশা চালান। যাদের পরিবার গ্রামে থাকে তারা আরও কম দিন চালান।
প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা কথা ছোট করে বলা যায়। আমরা প্রায়ই শুনি, বৃষ্টির দিনে, ঝড়ের দিনে রিকশাওয়ালারা ‘নবাব’ হয়ে যান। উনারা তখন ৫০ টাকার ভাড়া ১০০ টাকা এমনকি ১৫০ টাকা চেয়ে বসেন। এই ধরনের ‘অন্যায্যতায়’ আমরা খুব খেপে গালাগাল করি।
কিন্তু, এইখানে একটা অঙ্ক আছে। যারা চাকরি বাদে অন্য পেশায় নিয়োজিত তাদের সবসময় এই হিসাবটা করতে হয়। বৃষ্টির দিনে একজন রিকশাচালক তিনগুণ কামানোর সময় এই ঝুঁকিটা মাথায় নেন যে, যদি এই কারণে তার জ্বর বা অন্য অসুখ হয় তবে পরের অন্তত তিনদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হতে পারে। কামাই তো গেলই, সঙ্গে ওষুধপথ্যের ব্যাপার। অর্থনীতির ভাষায় একে বলে অপরচুনিটি কষ্ট বা সুযোগের খরচ। চাকরি করা সীমিত আয়ের মধ্যবিত্ত হয়তো বাড়তি ভাড়ার জন্য গালাগাল দেন, কিন্তু ঐ ভাড়াটাই অর্থনীতির ভাষায় রিকশাওয়ালার ‘রেইনি ডে’ ইনকাম, তার অসুখের ইনস্যুরেন্স।
রিকশা চালানোর মতো ‘ছুটা’ কাজের কোনো পেনশন হয় না, সাপ্তাহিক ছুটি নেই। আর ওপরে যেটা বললাম, একজন রিকশাচালক বছর দশেকের বেশি পূর্ণশক্তিতে রিকশা চালাতে পারেন না। এরপর চালালে তার কর্মক্ষমতা এবং সেইসঙ্গে আয় হ্রাস পায়।
রিকশাওয়ালার যেই সমস্যা তা বাসার কাজের বুয়া, ফেরিওয়ালাসহ প্রায় সমস্ত ছুটা কাজ, ইংরেজিতে যাদের বলে গিগ, তাদের মোকাবিলা করতে হয়। উনাদের কাজের ঘণ্টাপ্রতি হার, ছুটি এবং ইনস্যুরেন্সের হিসাবটা নিজেদেরই করতে হয়।
অন্যদিকে, ডেস্ক জব বা অফিস আদালতের কাজের ধরন ঠিক উলটো। এই ধরনের কাজে শরীরের শক্তির চেয়ে অভিজ্ঞতা জরুরি বলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপার্জন কিছু হলেও বাড়তে থাকে। মাসিক বাঁধা উপার্জন, অবসরের পর পেনশন এসবের নিরাপত্তা তো আছেই।
এখানে একটা জরুরি আলাপ চলে আসে। আমাদের দেশে দিনকে দিন প্রাইভেট চাকরিগুলো নিরাপত্তাহীন হয়ে যাচ্ছে। এই জায়গা থেকে মধ্যবিত্ত হতাশ হচ্ছে। কিন্তু, এই সমস্যা তো ট্রেড ইউনিয়ন না থাকা, মধ্যবিত্তের নিজেদের অধিকার আদায়ে রাজনীতি না করে নিরাপদে থাকতে চাওয়ার খেসারত। এই দায় তো নিম্নবিত্তের না। বরং বিশ্ব জুড়ে যখন মধ্যবিত্ত একটা ছিমছাম জীবন কাটাতে পারত তখন সে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত থেকে লড়াই করত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পুঁজিবাদী এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্রেও তাই হতো। বাংলাদেশেও নব্বইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ব্যাপারটা ছিল।
কিন্তু, নিও-লিবারেল অর্থনীতিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আমি গরিব, আমার দায় এই ধরনের ভুয়ো দর্শনে বিশ্বাস করে একে তো সে নিজের অধিকার থেকে বিস্মৃত হলো, অন্যদিকে হারিয়ে ফেলল জবাবদিহি করা এবং একত্র হওয়ার ক্ষমতা। অন্যদিকে, নারীবান্ধব সমাজ গড়তে না পারায়, মফিজের স্বল্পশিক্ষিত স্ত্রীর পক্ষে চাকরি-বাকরি করা সম্ভব হলো না। অন্যদিকে জবাবদিহিবিহীন রাষ্ট্র ও বাজার, পুঁজিবাদী যুক্তিতে বেপরোয়া হয়ে উঠল। বাসাভাড়া হোক বা দ্রব্যমূল্য, সবকিছুই কম আয়ের মানুষের নাগালের বাইরে যেতে লাগল।
এই অবস্থাতে বুয়ার পরিবারের আয় দেখে তার চোখ টাটাতে লাগল। অসহায় অবস্থায় এও ভাবতে লাগল, এর চেয়ে ভিক্ষা করলে বা বুয়ার কাজ করলে আয় বাড়ত। কিন্তু, সে নিজেও ভালো করে জানে, এ ব্যাপারটা অসম্ভব। সম্ভব হলে সে রিকশা চালাতেই নামত। বাড়ি বাড়ি বুয়ার কাজ করত। বাচ্চা ছেলেটাকে পড়ালেখা না করিয়ে হেলপারি করতে পাঠাত।
মধ্যবিত্ত কেন নিম্নবিত্তের সঙ্গে নিজের তুলনা করে আফসোস করবে না এর শেষ সুতাটা পাওয়া যায় ঐ বাচ্চাটার ভবিষ্যতের প্রশ্নে। ফেসবুকেই অনেকে জানাচ্ছেন কীভাবে বুয়া মাসে মাসে পয়সা জমিয়ে গ্রামে দুইএক ফালি জমি কিনছেন। কিছু সম্পদ করছেন। হেলপার রুবেলকে হয়তো তার বাবা-মা পড়ালেখা শেখাতে পারছেন না (এই ব্যাপারটাতেও রাষ্ট্রের দায় নিয়ে মধ্যবিত্তের কথা বলা উচিত) তবে তার জন্য তারা কিছু সম্পদ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সীমিত যে কর্মবছর সেই সময়ে কিছু সঞ্চয়ের চেষ্টা করছেন।
রুবেল যদি পড়াশোনা শিখে চাকরি-বাকরি নাও করতে পারে, আর যদি সে হেলপারির কঠিন জীবন পার করে পরে বাবা-মার মতো একটা সময় পর্যন্ত শারীরিক শ্রম দিতে পারে সেই উপার্জনের সঙ্গে এই সঞ্চয় যোগ করে সে আরেকটু সচ্ছল হবে বলেই অবচেতনে সুদূরপ্রসারী একটা স্বপ্ন দেখে পরিবারটি। তখন হয়তো রুবেলের ছেলে মাসুদ পড়ালেখা শিখবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। সাহেব-সুবোদের মতো অফিস করবে। সমাজে সম্মান পাবে।
অবশ্য, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন হচ্ছে তাতে রুবেলের ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আসতে পারবে কি না তা এক বড় প্রশ্ন। কিন্তু, এই সুদীর্ঘ আশাতেই পরিবারের সবাই অমানুষিক জীবন কাটাচ্ছে। সোজা কথায়, আজ মফিজ যেই অবস্থানে আছেন সেই অবস্থানের যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেও বুয়ার পরিবারের দুই প্রজন্ম লাগবে। সেই বুয়ার পরিবারকেই মফিজের হিংসা করা অর্বাচীনতা।
অন্যভাবে বলা যায়, হয়তো আজকের অনেক মফিজ আসলে সেই কষ্ট করা রিকশাওয়ালা আর হেলপারের উত্তরসূরি। যে কিনা নিজের অধিকার আদায়ের লড়াই ভুলে ভুল লক্ষ্যে রাগ ঝাড়ছে। হয়তো তার অবচেতন ধোঁকা খেয়েছে যে, সামাজিক সোপানের যে কয়েক পুরুষের স্বপ্ন তা আসলে রুদ্ধ হয়ে গেছে। পরিশ্রম দিয়ে যে মধ্যবিত্তের বেশি কিছু হওয়া যায় না এই সত্যটা জানার পর সেই ক্ষোভটাই সে ঝাড়ছে নিম্নবিত্তের দিকে।
যাদের আসলে পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার কথা ছিল।
লেখকঃ সাংবাদিক